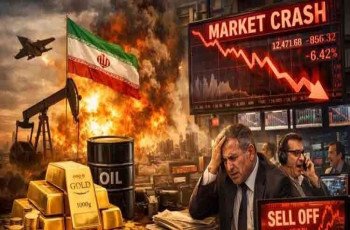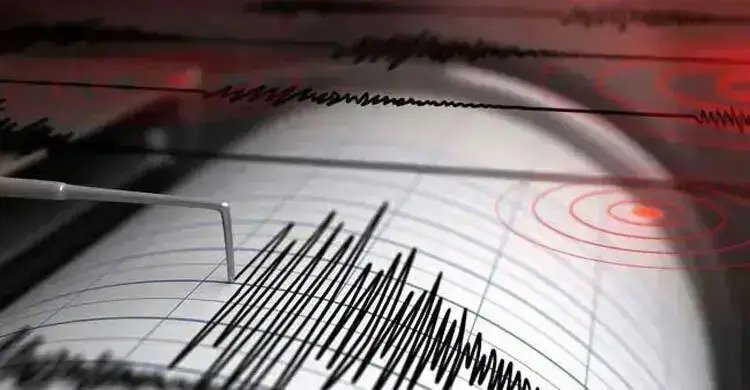অবশেষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জরুরিভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হলো। সোমবার (২৫ মার্চ) পাস হওয়া এই প্রস্তাবে গাজায় যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি হামাসের হাত থাকা জিম্মিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির শর্ত রাখা হয়েছে।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল ইসরায়েলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। তবে নিরাপত্তা পরিষদের বাকি ১৪টি দেশ প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়।
এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস হয়েছে। এই প্রস্তাব অবশ্যই বাস্তবায়ন হতে হবে। যদি কোনো পক্ষ এই যুদ্ধবিরতি ও এর শর্তগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়, তাহলে তা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের শামিল।
এর আগে শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির খসড়া প্রস্তাব দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু রাশিয়া ও চীনের ভেটোর কারণে প্রস্তাবটি পাস হয়নি। সেদিন মস্কোর অভিযোগ ছিল, ওয়াশিংটনের দ্বিমুখী নীতি ইসরায়েলের ওপর কোনো চাপ তৈরি করছে না।
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় ১১ দেশ। বিপক্ষে দেয় তিন দেশ। আর ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে একটি দেশ।
তবে জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া বলেছিলেন, এই খসড়াটি অত্যন্ত রাজনীতিকরণ করা হয়েছে ও এতে রাফায় সামরিক অভিযান চালানোর জন্য কার্যকর সবুজ সংকেত রয়েছে।